Source : BBC NEWS

এক ঘন্টা আগে
ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম, ‘রাজপথে ও সচিবালয়ে বিক্ষোভ করলে তদন্ত ছাড়াই চাকরি যাবে‘
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’ সংশোধন করতে যাচ্ছে, যাতে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।
এই খসড়া অনুযায়ী, কেউ রাজপথে বিক্ষোভ বা সচিবালয়ে অবস্থান কর্মসূচি করলে, তদন্ত ছাড়াই তাকে আট দিনের মধ্যে চাকরিচ্যুত করা যাবে।
এমনকি অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও চাকরি চলে যেতে পারে। যারা অন্যদের উসকানিও দেবে বা দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ভাঙবে, তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।
এই আইনে কর্মচারীকে দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া হবে, চাইলে ব্যক্তিগত শুনানিরও সুযোগ থাকবে, তবে এরপর চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে তিন দিনের মধ্যে চাকরিচ্যুতি সম্ভব।
অর্থাৎ সব মিলিয়ে আট দিনের মধ্যে চাকরি চলে যেতে পারে। প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে চাইছে।
সংশোধনীতে এমন ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে যাতে ২৫ বছর চাকরির আগে হলেও সরকার কাউকে নোটিশ দিয়ে অবসরে পাঠাতে পারে।
অনেক সরকারি কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে এবং ভিন্নমতকে দমন করতে ব্যবহৃত হতে পারে।
তারা আরও বলেন, আইন যেন কোনোভাবে অপব্যবহার না হয়, সেজন্য সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টির দরকার। এতে প্রশাসনের ভেতরে উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম, ”আশু বাস্তবায়নযোগ্য’ সব সুপারিশে একমত নয় ইসি‘
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কিছু সুপারিশকে ‘আশু বাস্তবায়নযোগ্য’ বলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে পাঠায়।
তবে ইসি জানায়, সব সুপারিশ তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। ইসি বলেছে, ফেরারি আসামি ও আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযুক্তদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণার মতো বিষয় রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া করা সম্ভব নয়।
আবার কিছু সুপারিশে আইনি সংশোধন ও রাজনৈতিক বিতর্ক নেই, তাই সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইসি সম্মত। যেমন—সশস্ত্র বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় যুক্ত করার প্রস্তাব।
এছাড়া রিটার্নিং ও প্রিসাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগের মতো সুপারিশও বাস্তবায়নযোগ্য। কিন্তু ব্যালট পেপারে জলছাপ রাখার মতো প্রস্তাবে আর্থিক খরচ থাকায় এখনই তা কার্যকর নয় বলে মনে করে ইসি।
ইসি আরও জানায়, নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, পোস্টাল ব্যালট এবং রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনার সুপারিশগুলোর মধ্যে কিছু চলছে, আর কিছুতে অর্থ জড়িত থাকায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।
১৮ মার্চ ইসি কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে ভিন্নমতও দিয়েছিল, কারণ এগুলোর ফলে কমিশনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
ফলে ইসি তিন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে—যেসব সুপারিশে তাত্ক্ষণিক বাস্তবায়ন সম্ভব, যেগুলোর জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য দরকার, এবং যেগুলো বর্তমান অবস্থাতেই ঠিক আছে।
সবমিলিয়ে ইসি বাস্তবতা ও সাংবিধানিক ভারসাম্য বিবেচনায় সুপারিশগুলো আলাদাভাবে মূল্যায়ন করেছে।

দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম, ’22 sectors still pay wages below poverty line‘ অর্থাৎ, ‘২২টি খাত এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে মজুরি দেয়’।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে অন্তত ২২টি খাতের শ্রমিক এখনো এমন বেতন পাচ্ছেন, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে।
শ্রম সংস্কার কমিশনের মতে, মাসে সাত হাজার ৮৬৯ টাকার কম আয় করলে কেউ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।
এই আয় দিয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব নয়। কমিশন বিশ্বব্যাংকের দুই দশমিক ১৫ মার্কিন ডলার দৈনিক আয় ও ২০১৭ সালের ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী এই সীমা নির্ধারণ করেছে।
বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ড ৪৭টি খাতের মজুরি পর্যালোচনা ও ন্যূনতম মজুরির সুপারিশ করেছে। তারা এসব খাতের প্রায় অর্ধেকই দারিদ্রসীমার নিচে মজুরি দিচ্ছে।
কম মজুরি পাওয়া খাতগুলোর মধ্যে আছে পেট্রোল পাম্প, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, আয়ুর্বেদিক কারখানা, ম্যাচ কারখানা, তুলা-বস্ত্রশিল্প ও বেকারি।
আর যেসব খাতে মজুরি দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে সেগুলো হলো ওষুধ শিল্প, গার্মেন্টস, ট্যানারি ও করাতকল।
বহু খাতে পাঁচ বছর পরপর বেতন নির্ধারণের নিয়ম থাকলেও, অনেক খাতে ৪২ বছরেও কোনো সংশোধন হয়নি।
শ্রমিকরা দিনে ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা কাজ করেও টিকে থাকা কঠিন বলছেন, তাই তারা ন্যূনতম ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা বেতন দাবি করছেন।
কমিশন সব খাতে একটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি চালুর প্রস্তাব দিয়েছে, যা কোনো খাতেই এর নিচে হবে না। এখন এ প্রস্তাব পর্যালোচনায় রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার রাজি হলে জাতিসংঘ রাখাইন রাজ্যে একটি মানবিক করিডোর চালু করতে পারে। তবে দুই দেশের অনুমতি ছাড়া জাতিসংঘ এককভাবে কোনো সহায়তা পাঠাতে পারবে না।
জাতিসংঘ বলেছে, রাখাইনে মানবিক পরিস্থিতি খুব খারাপ এবং তারা রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘ চায়, বাংলাদেশ হয়ে মিয়ানমারে সহায়তা পৌঁছাক।
এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হলেও শর্ত পূরণের কথা বলেছে। তবে বিএনপি ও অন্য বিরোধী দলগুলো বলছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, রাখাইন সীমান্ত এখন আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে এবং মিয়ানমার সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
ফলে বাংলাদেশকে পরিস্থিতি বুঝে সীমিত যোগাযোগ রাখতে হতে পারে। তবে রাষ্ট্রবহির্ভূত কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্ভব নয়।
সরকারের প্রেস সচিব বলেছেন, মানবিক করিডোর নিয়ে এখনো জাতিসংঘের সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি, তবে বাংলাদেশ প্রয়োজনে লজিস্টিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত।
রাখাইনে সহায়তা পাঠানোর উপযুক্ত পথ আপাতত বাংলাদেশই। জাতিসংঘের সহায়তায় এই উদ্যোগ রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
এই বিষয়টি জাতিসংঘ মহাসচিবের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরেও আলোচনায় এসেছিল, তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। সীমান্তে টানা ছয় দিন ধরে গুলিবিনিময় চলছে।
ভারত অভিযোগ করছে, পাকিস্তান বিনা উসকানিতে গুলি চালাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান বলছে, ভারতের চারটি যুদ্ধবিমানকে তারা তাদের আকাশসীমা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং ভারত যে কোনো সময় হামলা করতে পারে এমন গোয়েন্দা তথ্য তাদের হাতে আছে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানে অভিযান চালানোর পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। পাকিস্তানও সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্তে মহড়া চালাচ্ছে।
পাকিস্তান বলছে, তারা প্রথম আঘাত করবে না, তবে আক্রমণ হলে কঠিন জবাব দেবে। তারা একটি স্বচ্ছ তদন্তের প্রস্তাব দিলেও ভারত তা গ্রহণ না করে সংঘাতের পথ বেছে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে।
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দুই দেশের নেতার সঙ্গে কথা বলে উভয় পক্ষকে সংঘাত এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন।
পাকিস্তান ভারতের একতরফা সিদ্ধান্ত, যেমন সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিতের সমালোচনা করেছে।
এই পরিস্থিতিতে দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের উত্তেজনা শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, গোটা অঞ্চলের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
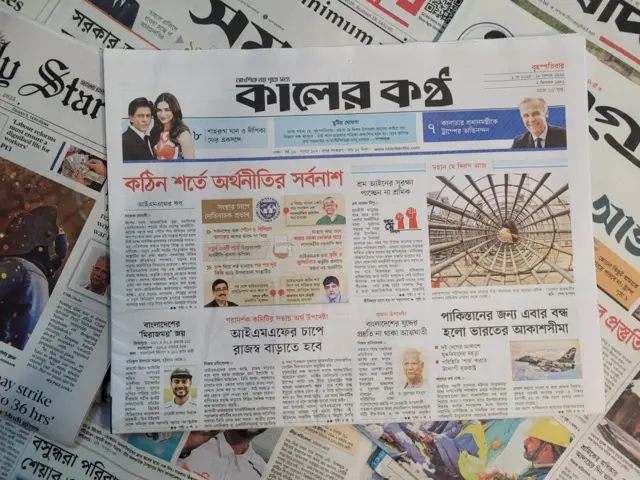
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে মাত্র চার দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিতে গিয়ে বাংলাদেশ কঠিন শর্তের জালে জড়িয়ে পড়েছে।
এই ঋণ পেতে গিয়ে সরকারকে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যার ফলে দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনগণের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
করছাড় ও ভর্তুকি কমিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিল্প খাতে বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, বেসরকারি খাতে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।
খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা কঠোর করায় ব্যাংক খাতে ঝুঁকি বেড়েছে। আইএমএফের একাধিক শর্ত বাস্তবায়ন করতে না পারায় ঋণের কিস্তিও আটকে যাচ্ছে। এতে সরকার ও বিশেষজ্ঞ মহলে ক্ষোভ বাড়ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আইএমএফ সব দেশের জন্য এক নিয়মে কাজ করে, কিন্তু বাংলাদেশে এই শর্তগুলো বাস্তবতা বিবেচনায় উপযোগী নয়।
কৃষি, জ্বালানি ও সামাজিক খাতে ভর্তুকি কমিয়ে দিলে তা সরাসরি সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। সরকার চাইলে এসব শর্ত মেনে না নেওয়ার সাহসিকতা দেখাতে পারে।
আইএমএফ চায় কর আদায় বাড়িয়ে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করতে, কিন্তু এতে ভোক্তার ওপর চাপ বেড়েছে। সব মিলিয়ে এই ঋণ দেশের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমকালের প্রধান শিরোনাম, ‘সরকার জাপানের সঙ্গে বিগ-বি বিগ-বি প্রকল্প নিয়ে এগোচ্ছে‘
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার জাপানের সঙ্গে “বিগ-বি” (বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট) প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়।
এই প্রকল্পটি প্রথমে ২০১৪ সালে বঙ্গোপসাগর ঘিরে শুরু করে জাপান এবং ২০২৩ সালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে।
যদিও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা জটিল, তবু বাংলাদেশ এই প্রকল্প চালিয়ে নিতে আগ্রহী। আগামী ১৫ই মে টোকিওতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক (এফওসি) হবে।
এই বৈঠকে বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকল্পে ভারতের যুক্ত হওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরা হবে।
মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিগ-বি প্রকল্প তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো—শিল্প ও বাণিজ্য, জ্বালানি, এবং পরিবহন।
এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করে পুরো অঞ্চলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে।
এই উদ্যোগ জাপানের মুক্ত ও উন্মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর কৌশলের অংশ। একইসঙ্গে চীনের প্রভাব ঠেকানো এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর বলয় জোরদার করাও এর উদ্দেশ্য।
রোহিঙ্গা সংকটসহ অন্যান্য আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ও বৈঠকে আলোচনার অংশ হবে।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান শিরোনাম, ‘China offers trade pact to boost investment, supply chain ties‘ অর্থাৎ, ‘বিনিয়োগ ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে চীন’
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, চীন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করার প্রস্তাব দিয়েছে, যা আগামী জুনে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫তম বৈঠকে সই হতে পারে।
একটির লক্ষ্য প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বাড়ানো, অপরটি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
চীন চায়, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতির মধ্যে এই সহযোগিতা দুই দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।
চীন মনে করে, সরবরাহ ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত না করে তা খোলা ও মুক্ত রাখা জরুরি।
চীনের এই উদ্যোগ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চীন বাংলাদেশে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে চায়।
চট্টগ্রামের আনোয়ারা, চাঁদপুর ও ভোলায় চীনের জন্য তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এপ্রিলে ঢাকায় একটি বৈঠকে এমওইউ-এর খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়।
চীন ১৯৯৬ সালের বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি হালনাগাদের প্রস্তাবও দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ চীনে মাত্র ৭১৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে, যেখানে আমদানি প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার।
চীন আগ্রহী কৃষিপণ্য সংরক্ষণের শীতল সরবরাহব্যবস্থা, ওষুধ, হালকা প্রকৌশলসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে। চীন আরও দুই বছর বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ঢাকা ট্রিবিউনের প্রধান শিরোনাম, ‘How can Dhaka solve its autorickshaw problem?‘ অর্থাৎ, ‘ঢাকা কীভাবে অটোরিকশা সমস্যার সমাধান করতে পারে?’।
প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ঢাকা শহরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
গত এক দশকে প্রচলিত সাইকেল রিকশাগুলোকে ব্যাটারি দিয়ে চালু করা হয়েছিল শ্রম কমাতে। কিন্তু এসব যানবাহন প্রায়ই দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে—এই মাসেই অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
চালকের অদক্ষতা, ট্রাফিক আইন না মানা, ব্রেক ঠিকমতো কাজ না করাসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।
অনেকেই বলছেন, সমস্যাটি যানবাহনের নয়, বরং প্রশিক্ষণহীন চালকদের কারণে হচ্ছে। তাই সরকার লাইসেন্স দিতে দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।
এই সমস্যা মোকাবেলায় বুয়েট একটি মানসম্পন্ন ‘ইজি বাইক’ ডিজাইন করেছে, যাতে নিরাপদ ব্রেক, দরজা, আলাদা যাত্রী ও চালক বসার ব্যবস্থা, নম্বর প্লেট ও ইলেকট্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে।
যানটি ছোট এবং ধীরে চলবে, যাতে শহরের সড়কে ভারসাম্য থাকে। এটি তৈরির প্রশিক্ষণ স্থানীয় মেকানিকদেরও দেওয়া যেতে পারে।
তবে পুরোনো অটোরিকশাগুলো একবারে বন্ধ না করে ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা, যাতে চালকদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
সরকারি সংস্থাগুলো এখন নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া তৈরি করছে। তবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে গণপরিবহন উন্নয়নই সবচেয়ে জরুরি বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।









